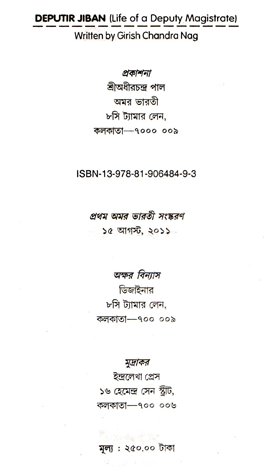ডেপুটীর
জীবন

Abujafar Shamsuddin
গিরীশচন্দ্র
নাগ
ডেপুটীর
জীবন
সম্পাদকীয়
গিরীশচন্দ্রের
আত্মজীবনীতে
অখন্ড
বঙ্গের
এক
পরিপূর্ণ
চিত্র
পাওয়া
যায়।
কর্মসূত্রে
তিনি
দেওঘর,
মালদা,
দিনাজপুর,
ময়মনসিংহ,
পূর্ণিয়া,
বরিশাল,
চট্টগ্রাম,
ঢাকা,
রাজমহল,
বড়পেটা,
গৌহাটি,
কোচবিহার
প্রভৃতি
বহু
অঞ্চলে
ঘুরে
বেড়িয়েছেন।
অর্থাৎ
এখনকার
ঝাড়খন্ড,
বিহার,
পশ্চিমবঙ্গ,
অসম
ও
বাংলাদেশের
বিভিন্ন
শহর
ও
সংলগ্ন
অঞ্চল
নিয়ে
বিস্তৃত
হয়েছিল
তাঁর
কর্মজীবন।
অখন্ড
বাংলা
প্রেসিডেন্সীর
বিভিন্ন
অংশের
ভূগোল
যেমন
বৈচিত্র্যময়,
তেমনি
তার
সমাজ,
অর্থনৈতিক
ব্যবস্থা
ও
সংস্কৃতি।
অরণ্য
ও
পর্বতময়
সাঁওতাল
পরগণা,
সমুদ্র
তীরবর্তী
চট্টগ্রাম,
শৈলশহর
দার্জিলিং,
বাংলার
বিস্তীর্ণ
নদীবিধৌত
সমতলভূমি,
অসমের
নিবিড়
অরণ্য
তাঁকে
প্রকৃতির
সঙ্গে
সখ্যতা
গড়ে
তুলতে
উদ্ধুদ্ধ
করেছে।
সেকথা
তিনি
লিখেও
গেছেন
বারংবার।
নানান
জনজাতির
সঙ্গে,
তাদের
ভিন্ন
ভিন্ন
সংস্কৃতির
সঙ্গে
পরিচিত
হওয়াও
তিনি
সৌভাগ্যের
কথা
বলে
মনে
করতেন।
বিস্তীর্ণ
অঞ্চলে
কর্মসূত্রে
ভ্রমণের
ফলে
তিনি
নিজেকে
ঋদ্ধ
করে
তুলতে
পেরেছিলেন।
সমসাময়িক
শিক্ষিত
বাঙালীর
মতো
তিনিও
অতীত
ইতিহাসের
প্রতি
আকৃষ্ট
ছিলেন।
প্রাচীন
প্রত্নঅবশেষ
বা
প্রত্নচিহ্নের
সন্ধান
পেলে
তিনি
কষ্ট
স্বীকার
করেও্
সেগুলি
পরিদর্শন
করতে
যেতেন।
এটি
অবশ্যই
তাঁর
সরকারী
কর্মের
অন্তর্ভুক্ত
ছিল
না।
রাজমহলের
নিকটস্থ
তেলিয়াগঢ়ী
দুর্গ,
মালদহে
অবস্থিত
বাংলার
প্রাচীন
দুই
রাজধানী
গৌড়
ও
পান্ডুয়ার
ধংসাবশেষ,
দিনাজপুরে
রায়গঞ্জের (এখনকার
উত্তর
দিনাজপুর
জেলার
সদর)
নিকটবর্তী
গণেশভিটা
(গিরীশচন্দ্র
এটিকে
রাজা
গণেশের
রাজধানী
বলে
উল্লেখ
করেছেন)
তিনি
আগ্রহ
সহকারে
দেখতে
গিয়েছিলেন।
সেকালে
ওইসব
অঞ্চলে
পথঘাটের
অভাব
ছিল।
প্রত্নস্থলগুলো
ছিল
বেশ
দুর্গম।
গিরীশচন্দ্র
সরকারী
কর্মের
ব্যস্ততা
সত্ত্বেও
ওই
অঞ্চলগুলি
বহু
সময়
নিয়ে
দেখেছিলেন।
প্রত্নস্থলগুলি
সম্পর্কে
তাঁর
মন্তব্যেও
নিজস্বতার
ছাপ
দেখা
যায়।
যেমন
বড়
বড়
দেওয়ানী
ও
ফৌজদারী
মোকদ্দমার
রায়
লেখার
সময়ে
নিজস্ব
বিচারবুদ্ধি
প্রয়োগ
করতেন
তিনি।
আত্মজীবনীর
অনেক
পৃষ্ঠাতেই
কিছুটা
আত্মমগ্ন,
মেধাবী
ও
চিন্তাশীল
এক
রুচিবান
মানুষের
পরিচয়
পাওয়া
যায়।
এই
কারণগুলির
জন্যই
গিরীশচন্দ্রের
আত্মজীবনী
বহু
পাঠকের
কাছে
আজও
আদৃত
হবে।
গিরীশচন্দ্রের
জীবন
ছিল
আনন্দ-বেদনা-হর্ষ-বিষাদের
চক্রবৎ
আবর্তনে
প্রভাবিত।
বহু
প্রিয়জনের
বিয়োগব্যথা,
চাকুরী
জীবনের
নানান
যন্ত্রণাময়
অভিজ্ঞতা
তাঁকে
যেমন
বিব্রত
করেছে,
তেমনি
সাময়িক
আনন্দের
কারণ
হিসাবে
কর্মকুশলতার
পুরষ্কার
লাভ (কখনও
কখনও
অভাবনীয়
বটে;
যেমন
লেজিসলেটিভ
কাউন্সিলের
সরকার
মনোনীত
সদস্য
হিসাবে
দিল্লীতে
স্থিত
হওয়া)
তাঁকে
উদ্ধেলিত
করেছে।
উনিশ
শতকের
এই
উচ্চপদাধিকারী
মানুষটি
কিন্তু
বিংশ
শতকের
তৃতীয়
দশকে
পৌঁছে
আত্মজীবনী
লিখতে
বসে
নিজের
জীবনকে
ব্যর্থ
বলেই
ঘোষণা
করেছেন।
উদ্যমী,
বিবেচক,
অতিথিপরায়ণ,
নীতিনিষ্ঠ
এবং
বাহ্যত
সফল
মানুষটি
সমাজ
ও
পারিপার্শ্বিকের
চাপে
ক্রমশ
হতাশ
ও
আত্মমুখী
হয়েছেন।
জীবনের
ঘটনা
পরম্পরাকে
ভবিতব্য
হিসাবে
বিবেচনা
করে
আত্মমগ্ন
হয়েছেন।
তার
আত্মজীবনী
বিশ্লেষণ
করলে
পাঠক
হয়তো
হেরোডোটাসের
কালোত্তীর্ণ
মন্তব্যটি
স্মরণ
করবেন Call no man happy
till you know the end of his life.
শেষজীবনে
অনিদ্রারোগ
ও
একাকীত্ব
তাঁর
নিত্যসঙ্গী
ছিল।
উনিশ
শতকের
দুমকা,
মালদা,
দেওঘর,
রাজমহলে
কর্মরত
উৎসাহী,
পরিহাসপ্রিয়
মানুষটি
ততদিনে
ব্যক্তিগত
বেদনায়
দীর্ণ।
তখনও
অবশ্য
তিনি
স্রোতের
বিরুদ্ধেই
হাঁটতে
চেয়েছেন।
সাহিত্যরচনায়
মনোনিবেশ
করে
অসাধারণ
এবং
অসামন্যকেই
আদর্শ
হিসাবে
প্রতিষ্ঠা
করতে
চেয়েছেন।
তাঁর
নিজের
ভাষায়: “গত
বৎসর
নিরবচ্ছিন্ন
বসিয়া
কার্য্যহীন
জীবনযাযপন
করা
অপেক্ষা
কিছু
সময়
লেখায়
ব্যয়
করার
একটা
প্রবৃত্তি
জন্মিল।
তাহার
ফলে
এই
বৎসরের
প্রথমদিকে
‘মনুয়া’
প্রকাশিত
হইয়াছে।
এই
গ্রন্থখানি
অনুন্নত
শ্রেণীর
নারীজীবনের
একটি
চিত্র।
শিক্ষা
ও
সংস্কার
দ্বারা
অসম্পৃশ্যা
নারীও
সমাজে
কিরুপে
আত্মপ্রতিষ্ঠা
লাভ
করিয়া
বৈধব্যজীবনে
অনাবিল
ব্রহ্মচর্য্য
পালন
করিতে
পারে
ইহাতে
তাহারই
দৃষ্টান্ত
প্রদর্শিত
হইয়াছে।”